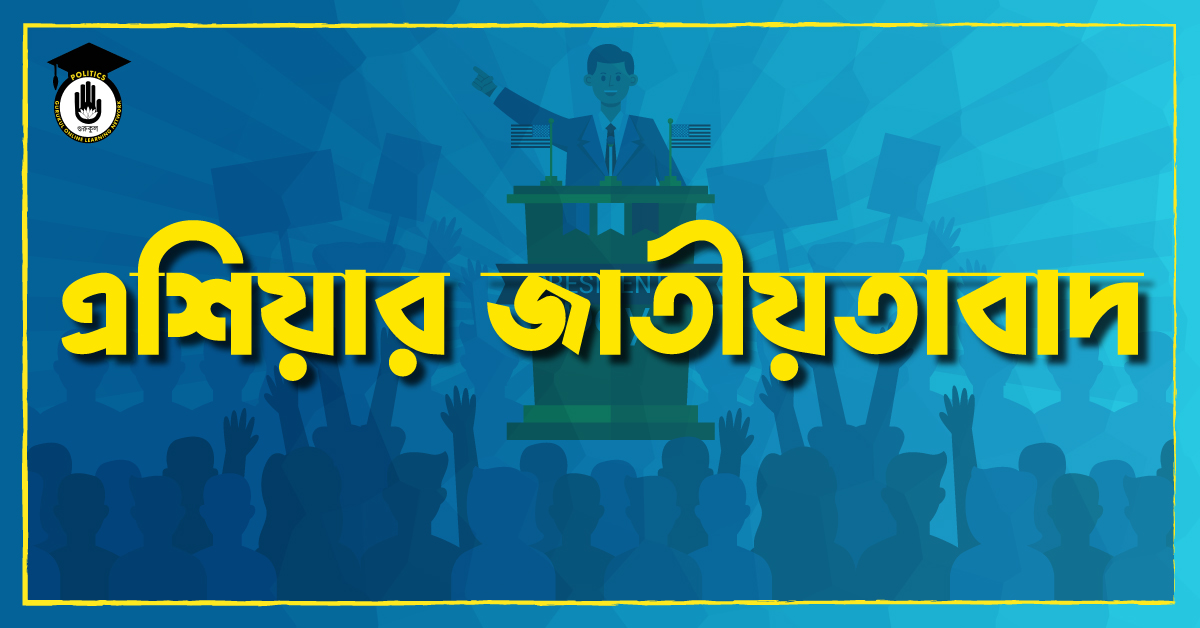এশিয়ার জাতীয়তাবাদ :
ঊনিশ শতকের শেষভাগেই এশিয়ার জনগণের মনে জাতীয়তাবাদের ধারণা উদ্ভূত হয়। বিশেষ করে, ১৮৮৫ সালে ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হলে জাতীয়তাবাদের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। সূচনালগ্নে ভারতের জাতীয়তাবাদীরা ইংরেজদের উদার রাজনীতির ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করে। যেভাবেই হোক, প্রথম মহাযুদ্ধ এশিয়ার ঔপনিবেশিক দেশগুলোয় জাতীয়তাবাদের হাওয়া বেশ প্রবল হয়ে ওঠে। গতিশীল জাতীয়তাবাদের ধারা প্রবল করেন কয়েকজন নিবেদিত প্রাণ নেতা। এঁদের মধ্যে তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক, মিশরের সা’দ জগলুল, সৌদি আরবের দ্বীপসমূহে ইবনে সউদ, ভারতে মহাত্মা গান্ধী এবং চীনে সান ইয়াৎ সেনের নাম উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আত্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বিশ্ব ভাবাদর্শের একটি বড় উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। আর এই কারণেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় জোরালোভাবে। এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে এশিয়া মহাদেশে এবং আফ্রিকায়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো এশিয়ার দেশগুলোতে প্রবাহিত জাতীয়তাবাদের ঘোড়ার লাগাম ধরতে ব্যর্থ হয়। ৪০ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে পর জাতীয়তাবাদের আদলে এশিয়াতে একটি পুনরুত্থান শক্তির উদ্ভব হয়। বিদেশি শক্তিকে পাশ কাটিয়ে, পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে ৯টি নতুন জাতি-রাষ্ট্রের উন্মেষ ঘটে, যেখানে পূর্বের কয়েক দশক ধরে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা বহাল ছিল। নতুন এই জাতি রাষ্ট্রগুলো হলো : ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, মায়ানমার, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন এবং কোরিয়া। ১

[ এশিয়ার জাতীয়তাবাদ ]
এশিয়াতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটার অন্য একটি কারণ হলো ধর্ম। বিভিন্ন দেশে ধর্মের প্রভাব সে দেশের শক্তি এবং রাজনৈতিক মেনিফেস্টোতে ভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে। যেমন, পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদের মেনিফেস্টোতে ধর্মের একটি বড় ভূমিকা ছিল। অবশ্য ধর্মের রাজনৈতিক এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব না থাকলে জাতিত্ববোধের অনুভূতি সৃষ্টি হয় না। এশিয়ায় জাতীয়তাবাদের মধ্যে একমাত্র জাপান ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। কারণ জাপানে জাতীয়তাবাদের আন্দোলনে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অংশগ্রহণ ছিল মূল বিষয়।
শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণির জাতীয়তাবাদী নেতারা মানুষের প্রতি গভীর মমতা এবং অনুভূতি প্রকাশ করতেন। গ্রামীণ জনগণ তাদের রাজনীতির প্রধান প্রবাহ জোরদার করবে— এটাই ছিল নেতাদের প্রত্যাশা, আর এই প্রত্যাশা পূরণ হলে দেশের জন্যও তারা হবে একটি বড় শক্তি। কিন্তু বাস্তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির শক্তি যেমন ছিল দুর্বল তেমনি তারা বিশ্বাস করতে পারেনি যে, তারাই জাতীয়তাবাদের আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে এবং নেতৃত্ব দিতে পারে।
১৯১৭ সালে সংঘটিত বলশেভিক বিপ্লব এবং প্রথম মহাযুদ্ধ এশিয়ায় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ। প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই পশ্চিমা শক্তি দুর্বল হতে থাকে। এর সুবাদে এশিয়ার শিল্পকরণ হয় এবয় ক্রমশ মধ্যবিত্ত শ্রেণি এতে সমৃদ্ধ হতে থাকে। অন্যদিকে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব জনগণের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বোধ আরও বাড়িয়ে দেয় এবং গণ-আন্দোলনের প্রভাব এশিয়াতে এমনভাবে পড়ে যে, এখানে জাতীয়তাবাদের বোধ খুব গভীরভাবে উপলব্ধ হয় এবং পশ্চিমা আধুনিক সমাজের সঙ্গে নিজেদের পার্থক্যটা বুঝে উঠতে পারে। ৪০
![জাতীয়তাবাদ [ Nationalism ]](https://politicsgurukul.com/wp-content/uploads/2022/02/Nationalism-জাতীয়তাবাদ-5-300x171.jpg)
এ কথা সত্য যে, এশিয়ায় ঔপনিবেশিক ইউরোপের পুঁজি ও সভ্যতা দুটোতেই উপকৃত হয়েছে। আগে যেমনটি বলা হয়েছে, শিল্প কারখানাগুলো প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কম উন্নত এলাকায়। উদ্দেশ্য, ঐ সব এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হবে, লোকেরা কলকারখানায় কাজ করে ভালো মজুরি পাবে এবং একই সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন দ্রুত হবে। কিন্তু এর পিছনে একটি অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করেই ব্রিটিশরা এসব উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হাতে নিয়েছিল। কাজেই এশীয়দের জীবনব্যবস্থা উন্নয়নের নামে যেমন দিয়েছে, তেমনি কৌশলে নিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। কলকারখানায় কোনো পণ্যের সম্পূর্ণ উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল না।
এখানে পণ্যের কাঁচামাল তৈরি হতো; সেগুলো নেওয়া হতো আবার ইংল্যান্ডে। সেখানে ‘ফিনিশড্ গুডস্’ তৈরি করে তা চড়াদামে এশিয়াতে এনে বিক্রি করা হতো। মার্কস এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলো হলো সাদা চামড়ার বুর্জোয়াদের নিজের দেশ উন্নয়নের একটি ক্ষেত্র।৪৫ উনিশ শতকের শেষ ভাগে এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে যে গণ-আন্দোলন গড়ে ওঠে দেশে দেশে, তাতে জাতীয়তাবাদের বীজাণু ছিল। কিন্তু এসব আন্দোলনে যারা জড়িত ছিলেন তাদের না ছিল জাতি গঠনের ধারণা, না ছিল সাংস্কৃতিক এবং আদর্শগত একতা সম্পন্ন গোষ্ঠীর ধারণা, যা থেকে একটি সম্পূর্ণ জাতিগঠন হতে পারে।
তুলনামূলক চিত্রে দেখা যায়, এশিয়া ও আফ্রিকায় জাতীয়তাবাদের ধারা প্রায় একই প্রবাহে অগ্রসরমান ছিল। কারণ, উভয় দেশই শ্বেতাঙ্গদের ঘৃণা এবং বিরোধিতা করত।৪৬ অর্থাৎ ইউরোপীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রধান বা প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গগুলো ধরে রেখেই এশীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশ সাধন করে, মুক্তভাবে জীবনযাপন করবে এটাই ছিল জনগণের আকাঙ্ক্ষা।
উপরের আলোচনার উপসংহারে প্রতীয়মান হয় যে, এশিয়া ও আফ্রিকার জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ছিল রাজনৈতিক ভাবাদর্শ পুষ্ট, আর এই ভাবাদর্শ তাদের উপনিবেশ বিরোধী মনোভাবের ফল।
Read More: